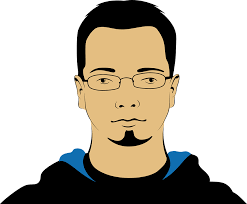


বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ খাতে সবচেয়ে আতঙ্কজনক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিকর রোগগুলোর একটি হলো ক্ষুরা রোগ বা ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ (এফএমডি)। প্রতিবছর এই ভাইরাসজনিত রোগে হাজার হাজার গরুসহ বিভিন্ন গবাদিপশু আক্রান্ত হয়। এতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হন খামারি ও কৃষকরা।
বয়স্ক গরুতে আক্রান্ত হলে উৎপাদন হ্রাস এবং বাছুর গরু আক্রান্ত হলে মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম এই রোগ। বাছুর গরুর জন্য খুবই মারাত্মক ব্যাধি এটি। এই রোগ শুধু পশুর স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি নয়, বরং দুগ্ধ উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা এবং পশুর রপ্তানি সম্ভাবনাকেও বাধাগ্রস্ত করে।
গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) মাইক্রোবায়োলজ অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. গোলজার হোসেন।
তিনি জানান, ক্ষুরা রোগ একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ, যা মূলত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং শুকরের মতো দ্বিখুরবিশিষ্ট প্রাণীদের আক্রমণ করে। এ রোগের ভাইরাসটি পিকোর্নাভিরিডি পরিবারের অ্যাপথো-ভাইরাস গণভুক্ত। এটি একটি সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড, পজিটিভ সেন্স আরএনএ ভাইরাস, যার সাতটি স্বতন্ত্র সিরোটাইপ রয়েছে। সেগুলো হলো— ‘ও’, ‘এ’, ‘সি’, ‘স্যাট-১’, ‘স্যাট-২’, ‘স্যাট-৩’ এবং ‘এশিয়া-১’। বাংলাদেশে প্রধানত ‘ও’, ‘এ’ এবং ‘এশিয়া-১’ সিরোটাইপের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।
তিনি আরো জানান, এই ভাইরাস সংক্রামিত পশুর লালা, দুধ, মলমূত্র, এমনকি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যেকোনো সংস্পর্শ, খাদ্য-পানীয় বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সুস্থ প্রাণীর দেহে প্রবেশ করতে পারে। রোগ ছড়াতে পারে এমন বাহক হতেও রোগ হতে পারে। যেমন: মানুষ, কুকুর, পাখি, যানবাহন ইত্যাদি।
ড. মো. গোলজার হোসেন বলেন, “বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমের পর এবং শীতের শুরুতে ক্ষুরা রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। আর্দ্রতা, জলাবদ্ধতা এবং খামারের অপর্যাপ্ত জীবাণুনাশ ব্যবস্থা এ সময় রোগ ছড়িয়ে পড়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।”
রোগের লক্ষণ হিসেবে ড. মো. গোলজার হোসেন আরো বলেন, “ক্ষুরা রোগের প্রধান লক্ষণগুলো হলো— জ্বর (আক্রান্ত পশুর তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে); মুখ, জিহ্বা, দাঁতের গাম বা নরম অংশ, ঠোঁট, ক্ষুর ও আক্রান্ত পশুর দুধের টিটে ফোস্কা হতে পারে; অতিরিক্ত লালা ঝরা; পা দিয়ে মাটি ঠোকানো বা খুঁড়িয়ে হাঁটা; দুধ উৎপাদন কমে যাওয়া; খাওয়ার অনীহা ও বিষণ্নতা; গরুর বাছুরের ক্ষেত্রে ‘টাইগার হার্ট’ নামক মারাত্মক হৃদরোগ দেখা যেতে পারে, এতে বাছুর হঠাৎ মৃত্যুবরণ করতে পারে।”
এ রোগের প্রতিকার হিসেবে এ গবেষক বলেন, “ক্ষুরা রোগের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। মূলত সহায়ক চিকিৎসা ও যত্ন দিয়েই আক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। মুখ এবং ক্ষুরের ক্ষতস্থানে জীবাণুনাশক দ্রবণ (যেমন- ১ শতাংশ অ্যাসিড সাইট্রিক বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট) দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হয়। ব্যথানাশক ও অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে সেকেন্ডারি ইনফেকশন ঠেকানো হয়। আক্রান্ত পশুকে আলাদা করে, নরম খাবার ও পর্যাপ্ত পানি দিয়ে বিশ্রামে রাখতে হয়।”
খামারিদের জন্য তিনি বলেন, “এ রোগ প্রতিরোধে খামারিদের বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। এর মধ্যে- বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত সিরোটাইপ অনুযায়ী নিয়মিত টিকা প্রদান; খামারে জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, খামারে বাইরের পশু প্রবেশ বন্ধ রাখা, যন্ত্রপাতি ও যান জীবাণুমুক্ত রাখা; নতুন পশুকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা (অন্তত ১৪ দিন); বিক্রয় ও স্থানান্তরের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা; খামারিদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে রোগের লক্ষণ, সংক্রমণ পদ্ধতি ও প্রতিরোধ সম্পর্কে অবগত হতে পারে।”
তিনি আরো বলেন, “খামারিদের কিছু ভুলের কারণে ক্ষতি বাড়তে পারে। যেমন- টিকা না দেওয়া বা অনিয়মিত টিকা দেওয়া; আক্রান্ত পশুকে আলাদা না রাখা; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব; খামার কর্মীদের সচেতনতার অভাব।”
সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক ও বাহরাইনে ‘স্যাট-১’ নামে নতুন এক সিরোটাইপ দেখা দেয়। যা পরবর্তীতে কুয়েত ও তুরস্কেও ছড়িয়ে পড়ে। এ অঞ্চলের জন্য এটি নতুন হওয়ায় প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে সুরক্ষা ব্যবস্থা আরো কঠোর করতে হবে ।
বাংলাদেশে ক্ষুরা রোগ গবাদিপশু খাতে অর্থনৈতিক ক্ষতির অন্যতম প্রধান কারণ। এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো প্রতিরোধমূলক টিকা, জৈব সুরক্ষা বজায় রাখা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি। সময়মতো সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই রোগের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব বলেও জানিয়েছেন এ অধ্যাপক।